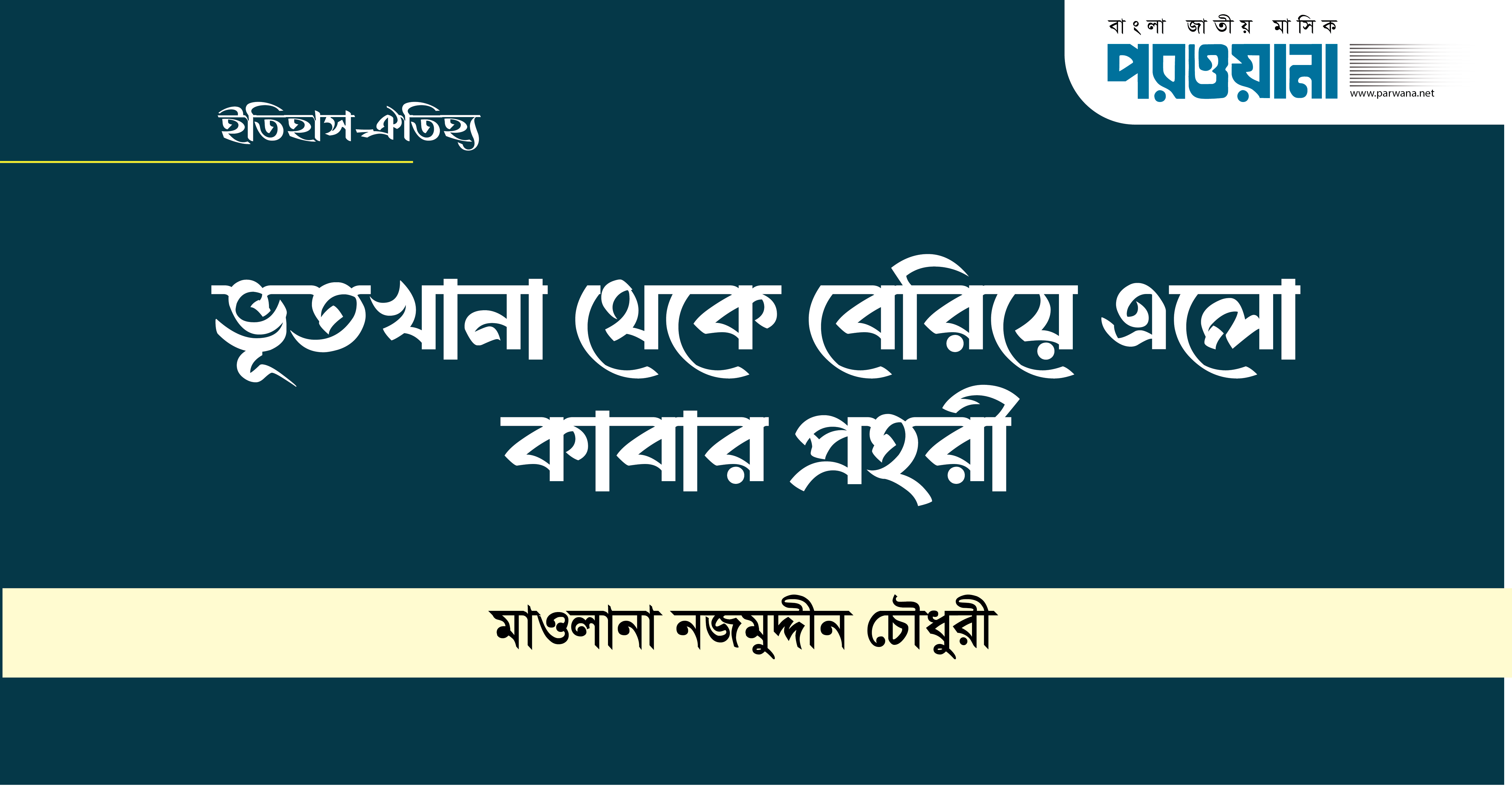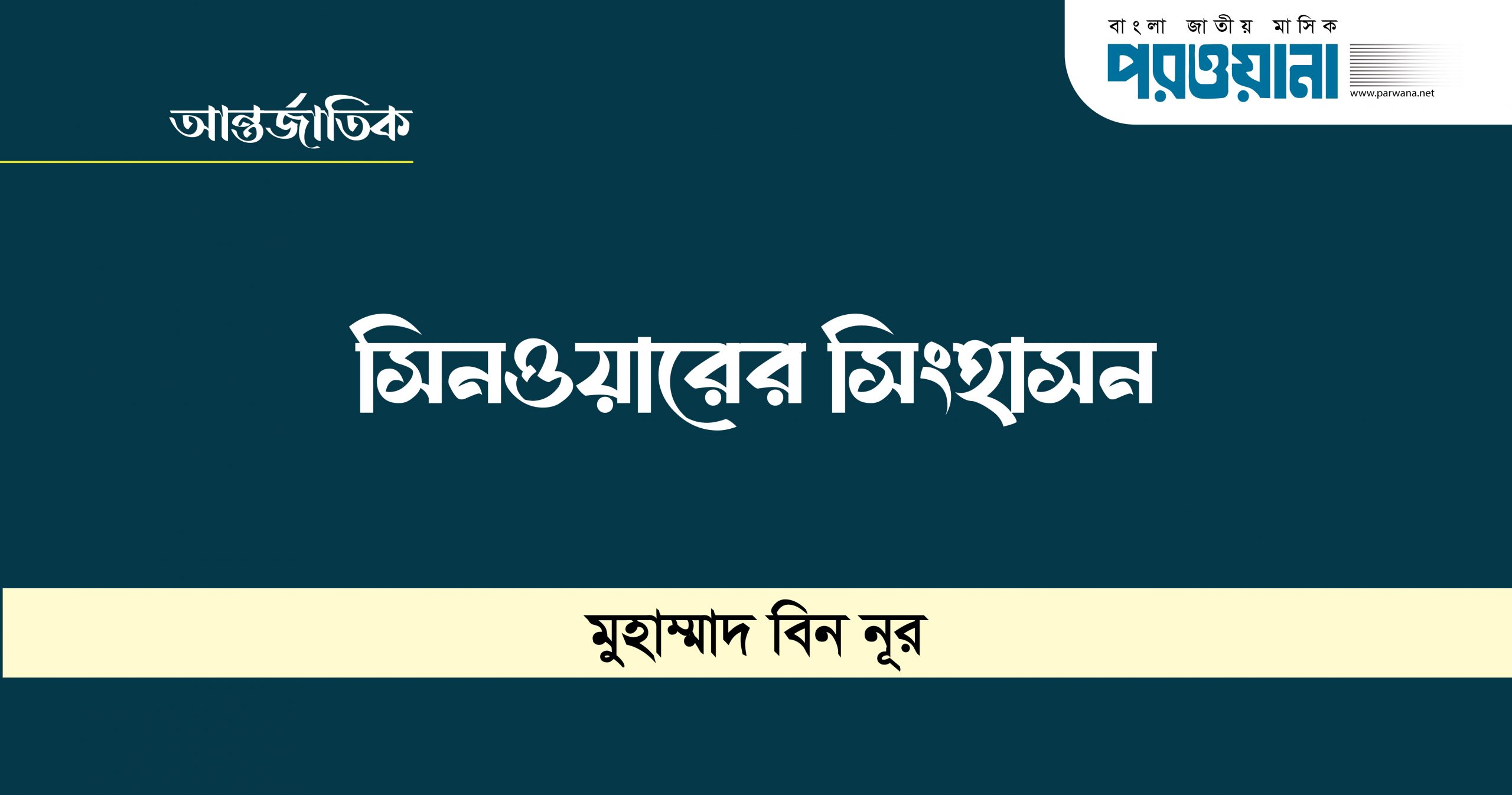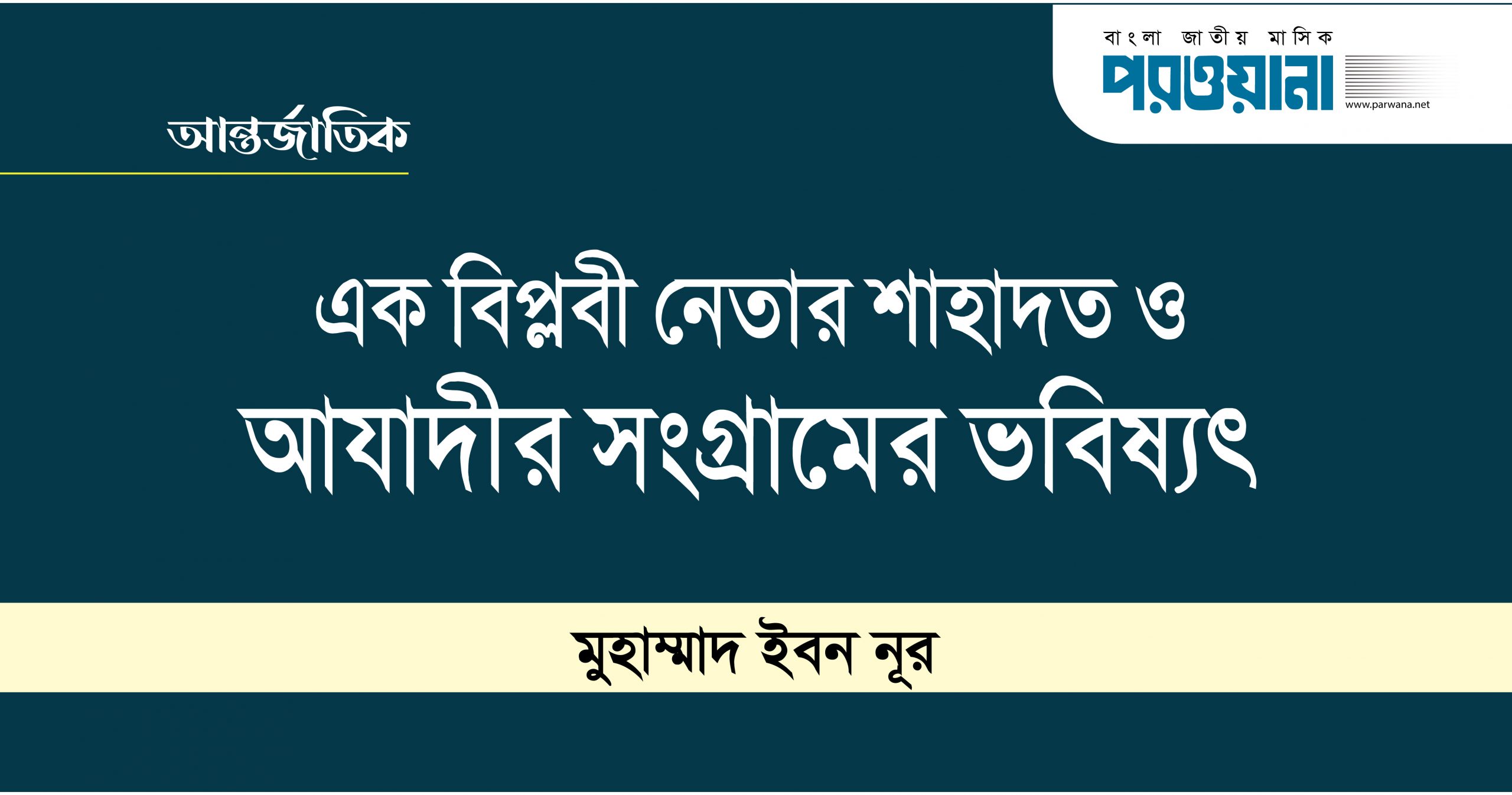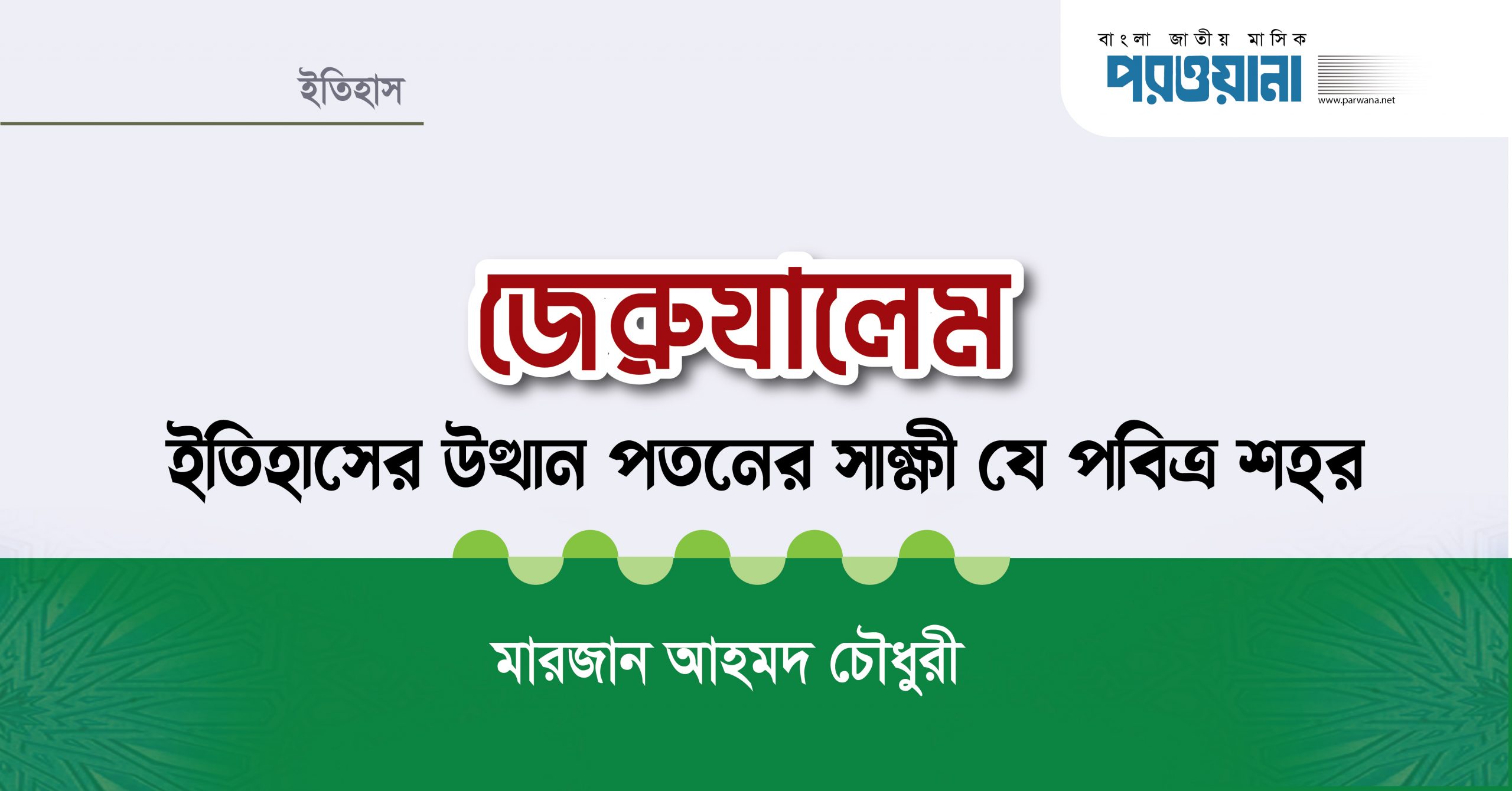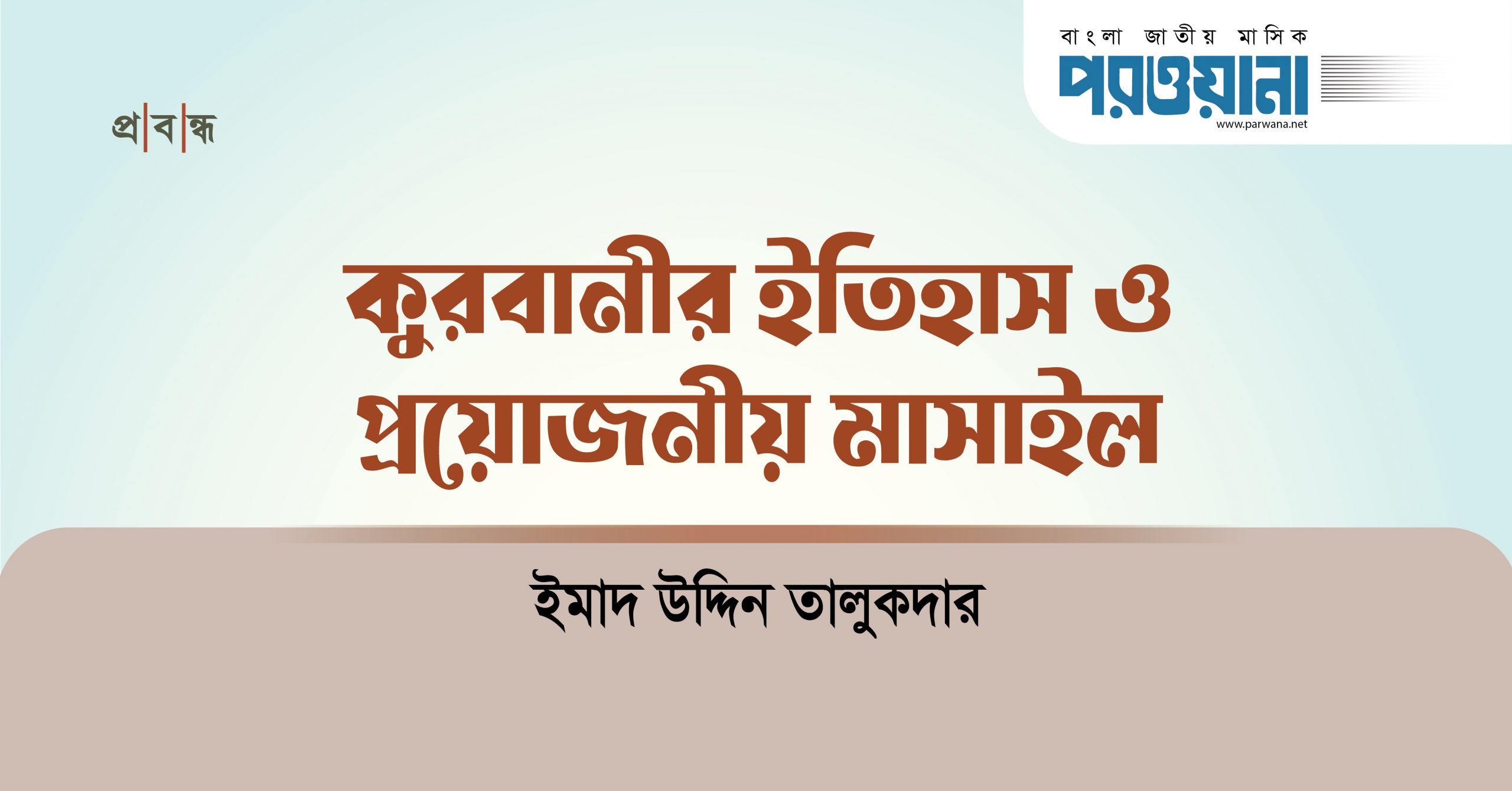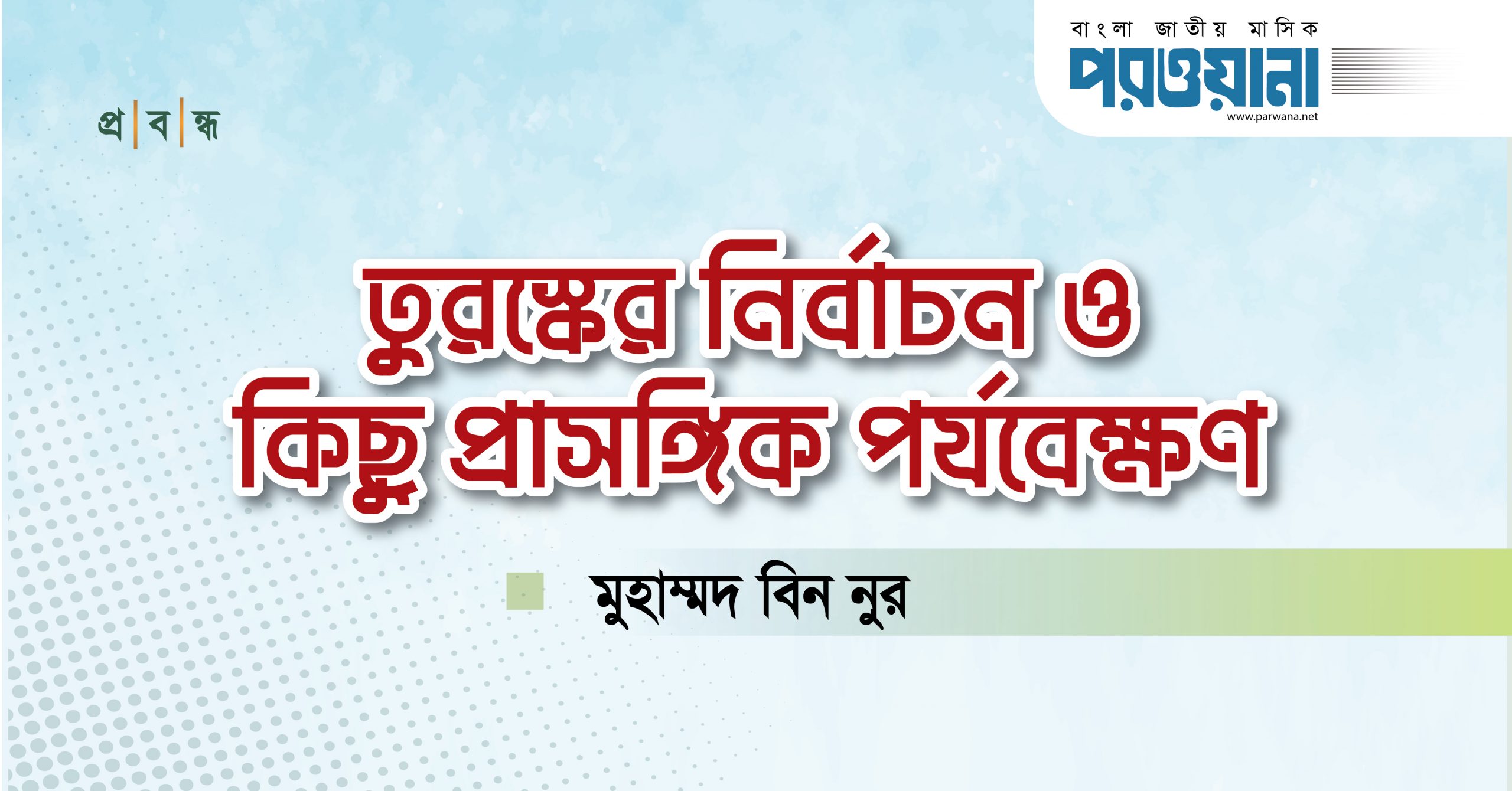যুদ্ধে যাওয়ার সময় এক ইসরায়েলি সৈন্যকে তার মা উপদেশ দিচ্ছেন, “শুনো, তুমি অনবরত যুদ্ধ করবে না। তাহলে ক্লান্ত হয়ে যাবে। একবার মাঠে যাবে, দু-একটি মুসলিম হত্যা করবে, এরপর ব্যারাকে ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবে।” ছেলে প্রশ্ন করল, “কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা যদি আমাকে মারতে আসে, তখন কী করব?” মা অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, “ওরা তোমাকে কেন মারবে? তুমি তাদের কী ক্ষতি করেছ?”
এটি হচ্ছে প্রায় শতাব্দীব্যাপী চলমান আরব-ইসরায়েল সংঘাতের একটি কৌতুকাবহ প্রতিচ্ছবি, যার পরতে পরতে আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর্যুপরি পরাজয়, লজ্জাজনক ব্যর্থতা ও মেরুদ-হীনতার কালো ছাপ লেগে আছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনীতিবিদরা শুরু থেকেই এই সংঘর্ষের নাম দিয়েছে আরব-ইসরায়েল সংঘাত। কিন্তু আপামর মুসলমানদের কাছে এটি মুসলিম উম্মাহ’র সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয় আরবের ভূমি কিংবা আরব জাতীয়তাবাদের পরাজয় নয়; বরং মুসলিম উম্মাহ’র পরাজয়। আরবরা ওখানে মুসলিম উম্মাহ’র প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। মুসলিম উম্মাহ’র কাছে ইসরায়েল ‘মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার’ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, মুসলিম উম্মাহ’র শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, অর্থাৎ আরব রাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেন এই ক্যান্সারকে অপসারণ করতে পারেনি? ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পরপরই আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্র মিসর, ট্রান্সজর্দান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, সৌদি আরব ও ইয়েমেন ইসরায়েলে আক্রমণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলোর এই প্রচেষ্টা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ইসরায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়। প্রশ্ন আসে, কেন? এই অবিরাম পরাজয়ের নেপথ্যে কারণ কী?
আসলে জয়-পরাজয় হুট করেই নির্ধারিত হয় না। প্রতিটি সফলতার পেছনে থাকে হাজারো পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সমন্বয় এবং সময় ও সুযোগকে কাজে লাগানোর গল্প, যেগুলো বহুলাংশে পর্দার আড়ালেই রয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটি ব্যর্থতার পেছনেও লুকিয়ে থাকে এমন শত শত কারণ, যা পরিসংখ্যানে দেখানো হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যমান বাস্তবতা হচ্ছে, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল নামক ইয়াহুদী রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরায়েল মোট ৫টি বড় যুদ্ধে জড়িয়েছে এবং প্রতিবারই উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো সংঘর্ষকে হিসেবে ধরলে সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে। তবে এ দৃশ্যমান বাস্তবতার পেছনেও ইসরায়েলের সফলতা ও আরবদের ব্যর্থতার শেকড় আরও গভীরে প্রোথিত, আরও ব্যাপক পরিসরে ব্যাপ্তিত। যায়নিস্ট আন্দোলনের সূচনা থেকে ইসরায়েল গঠন এবং ইসরায়েলের পরবর্তী সামরিক বিজয়গুলো ইয়াহুদী যায়নিস্টদের প্রায় এক শতাব্দীর রাতজাগা পরিশ্রমের ফসল। নয়তো সদ্য জন্ম নেয়া একটি অনাকাক্সিক্ষত রাষ্ট্রের কাছে জনবহুল আরব রাষ্ট্রগুলোর ভূমিধ্বস পরাজয় কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবতা তো বাস্তবতাই। আর সেই বাস্তবতা হচ্ছে, আরবরা ইসরায়েলের কাছে প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে। তাই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা ইসরায়েলের বিপক্ষে আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার কারণ খুঁজেছি।
শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা উচিৎ। যদিও পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে লেখা থাকবে যে, আরবরা ইসরায়েলের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু কথাটি চরম বিভ্রান্তিকর। ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে মোট ২১টি আরব রাষ্ট্র রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়ামান, ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মিসর, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, সুদান, জিবুতি, সোমালিয়া এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আফ্রিকান দ্বীপরাষ্ট্র কমোরোস। এই রাষ্ট্রগুলোর জনগণ ভাষাগত এবং (কিঞ্চিৎ) জাতিগতভাবে আরব হলেও এদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, জাতীয় স্বার্থ এবং ভূরাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, এই ২১টি আরব রাষ্ট্র (ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে) যদি একত্রিত হয়ে নিজেদের সামগ্রিক শক্তি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত, তাহলে ইসরায়েলের পক্ষে এক মুহূর্ত টিকে থাকার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই কখনও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। যে কয়েকটি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তন্মধ্যে অর্ধেকই ছিল প্রতীকী বা লোক দেখানো। উলটো মরোক্কো সেই প্রথম দিন থেকে ইসরায়েলের একনিষ্ঠ সমর্থক। তলে তলে সৌদি আরব, আমিরাত, ওমান ও বাহরাইন একই তাবুতে ঠাঁই নিয়েছিল। আজ এরা সবাই লজ্জার মাথা খেয়ে ইসরায়েলের কাছে বন্ধুত্বের নামে দান-দক্ষিণা চেয়ে বেড়াচ্ছে। কেবল ৪টি আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ করেছিল এবং ইসরায়েলের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল। এই রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে- মিসর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক। সুতরাং ইসরায়েল কখনও পুরো আরব বিশ্বকে পরাজিত করেনি, তারা পরাজিত করেছে আরব বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র (যদিও উল্লেখযোগ্য) অংশকে।
আরেকটি কথা না বললেই নয়। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, এ পর্যন্ত ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলোই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে হয়েছে। এবং অনেকে এটাও ধারণা করেন, এসব যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু এই দুইটি ধারণাই কার্যত ভুল। এ পর্যন্ত ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ৫টি বড় যুদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে কেবল প্রথম যুদ্ধের (১৯৪৮-৪৯) প্রতিপাদ্য ছিল ফিলিস্তিন এবং কেবল সে যুদ্ধেই আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। অন্য যুদ্ধগুলোর মূল কারণ ফিলিস্তিন ছিল না। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধ হয়েছিল সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে; ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ হয়েছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের তীব্র দ্বন্ধ এবং ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদের কারণে; ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ হয়েছিল সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমি নিয়ে; এবং ১৯৮২ সালের যুদ্ধ হয়েছিল লেবাননের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এই চারটি যুদ্ধেই ফিলিস্তিন ছিল খুবই গৌণ ইস্যু। ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের মতে, আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে আরবরাই বরাবর আগ্রাসি ভূমিকা অবলম্বন করেছে, এবং ইসরায়েল কেবল আত্মরক্ষার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কার্যত কেবল ১৯৪৮-৪৯ সালের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোকে আগ্রাসি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিসরের ওপর আক্রমণ করেছিল; ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল; ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক আগের যুদ্ধে দখলকৃত মিসরীয় ও সিরীয় ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধ করেছিল; এবং ১৯৮২ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল লেবাননের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। অর্থাৎ, আরব-ইসরায়েলি দ্বন্দ্বে প্রথম যুদ্ধটি ছাড়া বাকি প্রতিটি যুদ্ধে ইসরায়েল আগ্রাসি ভূমিকায় ছিল।
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে আরবদের ব্যর্থতার মূল চিত্রনাট্য রচিত হয়ে গিয়েছিল সেই ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম যুদ্ধেই। বাকি যুদ্ধগুলো কেবল প্রথম পরাজয়ের প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ব্রিটেন ফিলিস্তিন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে ইচ্ছুক ছিল, যে ফিলিস্তিন তারা দখল করেছিল উসমানী সালতানাতের কাছ থেকে। এজন্য তারা ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান করার জন্য জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ আহ্বান করে। ইতোপূর্বে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে থাকাকালীন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইয়াহুদীদেরকে বসবাস করার এবং ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়ে রেখেছিল ব্রিটিশ সরকার। প্রথমদিকে ব্রিটেনের এ পদক্ষেপে কারও পক্ষ থেকে তেমন কোনো সমর্থন লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হিটলারের দ্বারা চরম নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে ইয়াহুদীদের প্রতি বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে তিনভাগে বিভক্ত করার পক্ষে ভোট দেয়। সিদ্ধান্ত হয়, ফিলিস্তিনের ৫৬% ভূমিতে একটি স্বাধীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র এবং ৪৩% ভূমিতে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি আরব রাষ্ট্র স্থাপিত হবে। একই সাথে পবিত্র জেরুজালেম শহর একটি ‘আন্তর্জাতিক শহরে’ পরিণত হবে। ইয়াহুদীরা এই প্রস্তাব লুফে নেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি আরবরা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ‘আরব লীগ’ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কার্যত এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করাও আত্মমর্যাদার বিপরীত ছিল। কিন্তু আরবরা, কিংবা বৃহত্তর অর্থে বললে মুসলমানরা ভুলেই গিয়েছিল যে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করে শত্রুর সাথে এক টেবিলে বসে চুক্তি করার সক্ষমতা তারা বহু আগেই খুইয়ে ফেলেছে। মুসলমানরা নিজেদের ঈমান, ঐক্য, বল হারিয়ে ততদিনে ইউরোপের দয়াভিক্ষাকারী হিসেবে পরিণত হয়েছে। পরাজয়ের পেছনের যে গল্পটির কথা আমি আগের কলামে ইঙ্গিত করে এসেছিলাম, এটিই হচ্ছে সেই গল্প। আরবদের একটি বুনিয়াদি এলাকাকে কেটে-ছিড়ে ব্রিটেন ও জাতিসংঘ এর বৃহদাংশ ইয়াহুদীদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, অথচ মুসলমানরা কিছুই করতে পারছে না- এটিই ছিল মূল পরাজয়।
জাতিসংঘের ঘোষণার পর ফিলিস্তিনে ইয়াহুদী-আরব সংঘাত ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং একই দিনে ইয়াহুদী নেতা ডেভিড বেন গুরিয়ন স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। শুরু হয় মুসলিম গণহত্যা, যা চলেছিল পরবর্তী কয়েক বছর। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পরদিনই মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়ামানের সৈন্যরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া।
যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আরব রাষ্ট্রগুলো আংশিক সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু ইসরায়েলিরা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দু’দফা জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে শুরু করে। আরব সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করে এবং ইসরায়েলিরা একের পর এক অঞ্চল দখল করতে থাকে। ইসরায়েলিদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ১৯৪৯ সালে একে একে যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিসর, মার্চে লেবানন, এপ্রিলে জর্ডান এবং জুলাইয়ে সিরিয়া ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর মধ্য দিয়ে প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে এবং জাতিসংঘ তাদেরকে ফিলিস্তিনের যে ৫৬% ভূমি প্রদান করেছিল, সেটি তারা নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়। এর পাশাপাশি জাতিসংঘ ফিলিস্তিনি আরবদেরকে ফিলিস্তিনের যে অংশ প্রদান করেছিল, তার প্রায় ৬০% ভূমিও ইয়াহুদীরা দখল করে নেয়। পশ্চিম জেরুজালেম ইসরায়েলের হস্তগত হয়। অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জর্ডান ও মিসরের এই যুদ্ধে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং এই যুদ্ধের সময় জর্ডান ৫,৬৫৫ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং এগুলোকে নিজস্ব ভূমি হিসেবে ঘোষণা করে। মিসর ৩৬৫ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট গাজা ভূখ- দখল করে। গাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে না নিলেও এ অঞ্চলটি মিসরের সামরিক উপনিবেশে পরিণত হয়।
এবার আসে এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় শক্তিশালী হয়েও কেন এই যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী যুদ্ধসমূহে পরাজিত হয়েছিল? এর নানাবিধ কারণ রয়েছে।
প্রথমত, ৭টি আরব রাষ্ট্র এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরায়েলি সৈন্যসংখ্যা ছিল আরবদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪৮-৪৯ এর যুদ্ধে ইসরায়েল মোট ১,১৭,৫০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছিল। ওদিকে ৭টি আরব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে মাত্র ৫১,১০০ থেকে ৬৩,৫০০ সৈন্যকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি ২ জন ইসরায়েলি সৈন্যের বিপরীতে মাত্র ১ জন আরব সৈন্য ছিল। এবং এটিই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কম, তারা তুলনামূলকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।
শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ করেছিল মিসর, ইরাক, জর্ডান এবং সিরিয়া। লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী বা লোক দেখানো। যুদ্ধের সময় মিসর ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিল প্রায় ২০,০০০ সৈন্য, ইরাক প্রেরণ করেছিল প্রায় ১৮,০০০ সৈন্য, জর্ডান প্রেরণ করেছিল প্রায় ১০,০০০ সৈন্য এবং সিরিয়া প্রেরণ করেছিল প্রায় ৫,০০০ সৈন্য। অপরদিকে মাত্র ১,২০০ সৌদি এবং ৩০০ ইয়ামানি সৈন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে সংঘটিত একটি খণ্ড-যুদ্ধ ছাড়া কার্যত লেবানন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি।
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলোর কি যুদ্ধক্ষেত্রে এরচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য প্রেরণের সামর্থ্য ছিল না? জবাব হচ্ছে, তাদের সামর্থ্য ছিল, কিন্তু সেই সামর্থ্যকে তারা কাজে লাগায়নি। কারণ, ফিলিস্তিন বা ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা কখনও এই আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাকের ফিলিস্তিন সংক্রান্ত নিজস্ব স্বার্থ ছিল, এজন্যই তারা ফিলিস্তিনে তুলনামূলকভাবে বড় সৈন্যদল পাঠিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে লেবাননের এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সৌদি আরব ও ইয়ামানের ফিলিস্তিন নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এজন্য তারা নামকাওয়াস্তে এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে দায় সেরেছিল।
দ্বিতীয়ত, একে তো আরবদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কম, তদুপরি আরব সৈন্যদের তুলনায় ইসরায়েলি সৈন্যদের মনোবল ছিল অনেক বেশি। এ মনোবলই দুই দলের মধ্যে সমুদ্রসম পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। মাত্র কয়েক বছর আগেই ইয়াহুদীরা ইউরোপে ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হয়েছিল। সেই আতঙ্কের রেশ তাদের মধ্যে তখনও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। আরব রাষ্ট্রগুলো যখন ইসরায়েলকে আক্রমণ করে, তখন ইসরায়েলিদের অনেকেই এই ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিল যে, তারা নতুন করে একটি গণহত্যার শিকার হতে যাচ্ছে। ফলে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত সামর্থ্য ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যদের এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। অন্তত ইয়াহুদীদের ন্যায় এই যুদ্ধে প্রাণ রক্ষার কোনো তাগিদ আরব সৈন্যদের মধ্যে ছিল না, থাকার কথাও নয়। স্বভাবতই তারা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে লড়াই করার প্রচেষ্টা চালায়নি। এটি তাদের পরাজয়ের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
তৃতীয়ত, ইসরায়েল ছিল একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। এজন্য তাদের কাছে এই যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয়কে একটি ‘অতিমানবীয়’ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্থিতিশীল ছিল না। এদের মধ্যে মিসর ১৯২২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু কার্যত এই যুদ্ধের সময়েও মিসর ছিল ব্রিটেনের একটি আধা-উপনিবেশদ । ১৯৫২ সালের পূর্বে মিসর প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। ইরাক ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়, কিন্তু কার্যত ইরাকও এই যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের একটি আধা-উপনিবেশই ছিল। ১৯৫৮ সালের পূর্বে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। অনুরূপ সিরিয়া ও লেবানন যথাক্রমে ১৯৪৫ ও ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ১৯৪৬ সালের আগে তারা প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি। জর্ডান কেবল ১৯৪৬ সালেই ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, এবং এই যুদ্ধের সময়েও জর্ডানের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ছিলেন ব্রিটিশ। সৌদি আরব ও ইয়ামান রাজ্য দুইটি যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময়ে এরাও সেরকম অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। সুতরাং, প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল কার্যত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং আধা-উপনিবেশ প্রকৃতির কতিপয় আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এজন্য গুণগতভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তার ওপর ইসরায়েলি সৈন্যদের মধ্যে এরকম বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের আধুনিক যুদ্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ছিল। অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতা আরব রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যদের ছিল না।
চতুর্থত, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, ইসরায়েলের প্রকৃত সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলোর কোনো ধারণা ছিল না। বিশেষত মিসরের রাজা ফারুক এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি শুকরি আল-কুওয়াতলির উপদেষ্টারা তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন, যুদ্ধে আরবরা সহজেই বিজয়ী হতে পারবে। তাই মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধে এসেছিল এক প্রকার অন্ধ অবস্থায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়াটাই ছিল তাদের জন্য স্বাভাবিক।
পঞ্চমত, আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের সময় তাদের সামরিক কার্যক্রম সমন্বিত করতে পারেনি। ফলে একটি যৌথ সামরিক অভিযানের পরিবর্তে এটি এক একটি বিচ্ছিন্ন সামরিক অভিযানে পরিণত হয় এবং ইসরায়েলিরা একে একে প্রতিটি আরব সৈন্যদলকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে। দেখা গেছে মিসর যখন পশ্চিম দিক থেকে ইসরায়েলে আক্রমণ করেছে, পূর্বদিকের জর্ডান ও উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত সিরিয়া তখন আক্রমণ না করেই বসে আছে। আবার যখন ইসরায়েল সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে, তখন মিসর হাত গুটিয়ে বসে আছে। এই অহেতুক অকর্মণ্যতা ইসরায়েলকে বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছিল।
আরবদের সমন্বয়হীনতার মূল কারণ ছিল তাদের পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের ফিলিস্তিন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল। জর্ডানের রাজা প্রথম আব্দুল্লাহ নিজেকে সমগ্র ‘উর্বর অর্ধচন্দ্র’ (ঋবৎঃরষব ঈৎবংপবহঃ) অঞ্চলের শাসক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন দখল করতে ইচ্ছুক ছিলেন। যুদ্ধে জর্ডানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের যত বেশি সম্ভব ভূমি দখল করে নেওয়া এবং নেগেভ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ট্রান্সজর্ডানের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ চলাকালে এ বিষয়ে জর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্যে গোপন সমঝোতা হয়েছিল। ইরাক এক্ষেত্রে জর্ডানকে সমর্থন করেছিল। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে, জর্ডানের রাজপরিবার মক্কার শরীফ (সায়্যিদ) বংশের অংশ। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় মক্কার শাসনকর্তা শরীফ (সায়্যিদ) হুসাইন ইবন আলী ব্রিটিশদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উসমানী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যেরকম বিদ্রোহ দেড়শ বছর আগে করেছিলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব নজদী ও মুহাম্মদ ইবন সৌদ। সেবার পুরস্কারস্বরূপ নজদীরা নজদ এলাকার কর্তৃত্ব পেয়েছিল। এবার পুরস্কারস্বরূপ উসমানী সালতানাত ভেঙ্গে যাওয়ার পর ব্রিটিশরা হুসাইন ইবন আলীর বড় পুত্র আলীকে হিজাযের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় সেই ব্রিটিশদের সহযোগিতায় আবদুল আযীয ইবন সৌদ মক্কার শাসনকর্তা (যিনি নিজেকে রাজা বলতেন) আলী ইবন হুসাইন ইবন আলীকে সরিয়ে দিয়ে মক্কা দখল করে নিয়েছিলেন। শরীফ হুসাইন ইবন আলীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ, যাকে ব্রিটিশরা উপহারস্বরূপ জর্ডানের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। তার বংশধররা এখনও জর্ডান শাসন করছেন। শরীফ হুসাইন ইবন আলীর তৃতীয় পুত্র ছিলেন ফায়সাল, যাকে ব্রিটিশরা উপহারস্বরূপ ইরাকের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ইরাকের সেনাবাহিনী ফায়সালের পুরো পরিবারকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। ইতিহাস কখন কার ভাগ্যে পাল্টায়, বলা মুশকিল।
অন্যদিকে, মিসরের রাজা ফারুক নিজেকে সমগ্র আরব বিশ্বের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ফিলিস্তিনের অংশবিশেষ দখল করে নেওয়া। ট্রান্সজর্ডানের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব মিসরকে সমর্থন দিচ্ছিল। রাজা ফারুকের পরে মিসর যখন জামাল আবদুল নাসিরের হাতে এসেছিল, তখন মিসর থেকে আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগান উঠেছিল। নাসিরের একটি পদক্ষেপও ইসলাম কিংবা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল না। বরং তিনি সবই করেছিলেন তার তথাকথিত আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গতি দেয়ার জন্য। অনুরূপ সিরিয়া ও লেবাননের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ফিলিস্তিনের অংশবিশেষ দখল করে নেওয়া। প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে সিরিয়া ছিল ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সদ্য স্বাধীন দেশ। পরবর্তীতে বাথ পার্টির নেতৃত্ব সিরিয়া একটি অতি-সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল এবং সকলেই একে অপরকে তীব্র সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। এমতাবস্থায় কোনো জোটই কার্যকরী হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে আরব জোটও কার্যকরী কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। উল্টো কলেবর বাড়িয়ে বদনাম ডেকে এনেছে।
ষষ্ঠত, ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, যা আরব রাষ্ট্রগুলোর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র উপস্থিত ছিল না। ইসরায়েল সরকার ও সামরিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন একটা খবরদারি করত না, এখনও করে না। বরং মাঠ পর্যায়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা এবং আচমকা আপতিত পরিস্থিতি মুকাবিলায় মাঠের নেতারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে করে ইসরায়েল সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে গতি হারাতে হয় না। পক্ষান্তরে আরব রাষ্ট্রগুলো তখনও এবং আজও চরম একনায়কতন্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। তাই তাদের সেনাবাহিনীও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি ছোটখাটো সিদ্ধান্ত একেবারে সরাসরি রাজপ্রাসাদ থেকে আসতে হয়। এতে করে আচমকা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বদলে আরব সেনাবাহিনীকে রাজা-বাদশার মর্জির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আরব রাষ্ট্রগুলোর সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে চলমান দুর্নীতি এক্ষেত্রে আরও বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ পরবর্তী গবেষণায় উঠে এসেছে, মিসর সরকার তাদের সশস্ত্রবাহিনীকে নি¤œমানের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যাগত আধিক্য ও দৃঢ় মনোবলের পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও গুণগত আধিপত্য অর্জন করে আরবদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।
সপ্তমত, ইসরায়েল প্রথম দিন থেকেই একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা ব্যবস্থা তৈরি করতে মনোনিবেশ করেছিল। প্রথমদিকে নাতিভ ও লেকেম নামে ইসরায়েলের দুটি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। আজকে সেগুলো উন্নত হয়ে মোসাদ, আমান ও শাবাক নামে তিনটি বিশ্বমানের গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ধারণা আছে অথচ মোসাদের নাম শুনেননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকের ইসরায়েল টিকে থাকার পেছনে মোসাদের অবদান কতটুকু, তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আরব রাষ্ট্রগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল না। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দেখা গেছে, মিসর ইসরায়েলে হামলা করার জন্য উপযুক্ত স্থানে যুদ্ধবিমান জড়ো করেছে। যেদিন হামলা করবে, তার আগের রাতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান এসে মিসরের বিমান বাহিনীর স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। শুধু সেদিনের কথা নয়; বরং আজকের দিনেও পাকিস্তান ও তুরস্ক ব্যতীত মুসলিম বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বহিঃবিশ্বে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করার মতো শক্তিশালী কোনো সংস্থা নেই।
অষ্টমত, যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েল বহির্বিশ্বের সমর্থন ও অস্ত্র-সহযোগিতা লাভ করেছিল, আজও করে আসছে। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো অনুরূপ কোনো সমর্থন বা সহযোগিতা লাভ করেনি। তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই চোখ-কান বন্ধ করে ইসরায়েলের পক্ষপাতিত্ব করে আসছে। অর্থ, প্রযুক্তি, অস্ত্র সব দিক থেকেই ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি মদদপুষ্ট। যুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘ উভয় পক্ষের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া প্রথমদিকে সোভিয়েত মিত্ররাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়াও ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করত। আরব রাষ্ট্রগুলো অনুরূপভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেনি।
এই ৮টি কারণ ছিল বাহ্যিক, যা ইসরায়েলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর্যুপরি পরাজয়ের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণগুলো যে কোনো সমর-বিশেষজ্ঞের গবেষণায় পাওয়া যাবে। আমিও এগুলো রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমরবিদদের গবেষণা থেকে সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এর বাইরেও আরব রাষ্ট্রগুলোর বারংবার ব্যর্থতার একটি বড়, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, যা কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা সমরবিদদের লেখনিতে আমি খুঁজে পাইনি। পেয়েছি আল্লাহর পাক কালাম কুরআন শরীফে। সেই কারণটি হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্যের অনুপস্থিতি।
আরব রাষ্ট্রগুলো এসব যুদ্ধে জড়িয়েছিল প্রধানত নিজেদের স্বার্থে। কারও স্বার্থ ছিল ভূমি দখল করে নিজেদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা, কারও স্বার্থ ছিল বিরোধী কোনো আরব রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করা, কারও স্বার্থ ছিল আরব জাতীয়তাবাদ। একে অন্যের প্রতি তীব্র সন্দেহ ও অনাস্থা পোষণ করত। মুসলিম উম্মাহ’র ধারণা (ঈড়হপবঢ়ঃ) ভেঙ্গে ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকে ভৌগলিক বা নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের যে পাঠ পড়িয়েছিল, সেটি ছিল আরবদের কাছে ধর্মগ্রন্থের ন্যায় পূজ্য। একটি আরব রাষ্ট্রও ইসলামের জন্য যুদ্ধে যায়নি। ভাবখানা এমন, যেন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা নেহায়েত লজ্জার বিষয়। এমনকি নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য কেবল প্রথম যুদ্ধেই খানিকটা তাড়না ছিল। পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বার্থ আরবদের কাছে খুবই গৌণ ছিল। অথচ আরবরা ভুলে গিয়েছিল যে, আল্লাহ পাক একটিবারও আরবের ভূমি, আরব রাজা-বাদশাদের ক্ষমতালিপ্সা কিংবা আরব জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করার ঘোষণা দেননি। বরং ঘোষণা দিয়েছেন মুসলমানদেরকে সাহায্য করার। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ -আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার দায়িত্ব। (সূরা আর-রূম, আয়াত-৪৭)
তোতাপাখির মতো পশ্চিমাদের শেখানো বুলি মুখে নিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধগুলোকে আরব-ইসরায়েল সংঘাত ভেবেছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভৌগলিক কর্তৃত্ব এবং নিপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনদের রক্তের বিনিময়ে পশ্চিমাদের সন্তুষ্টি কিনতে বসেছিল। তাই তারা ‘মুসলিম’ হিসেবে যুদ্ধে যায়নি, গিয়েছিল ‘আরব’ হিসেবে। ফলাফলস্বরূপ যৎসামান্য কিছু ইয়াহুদীর কাছে বারবার মুখ কালো করে ফিরে এসেছে। ঈমানের দুর্বলতা আরবদের মুখে বারবার পরাজয়ের কালিমা লেপন করে দিয়েছে। আজ যখন আরব রাষ্ট্রগুলো এক এক করে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেই ঘোষণার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে মিশে আছে উপর্যুপরি পরাজয়, লজ্জাজনক ব্যর্থতা ও মেরুদ-হীনতার কালো ছাপ।