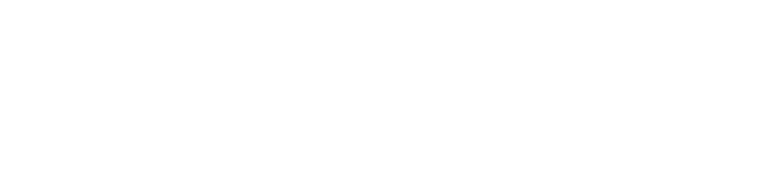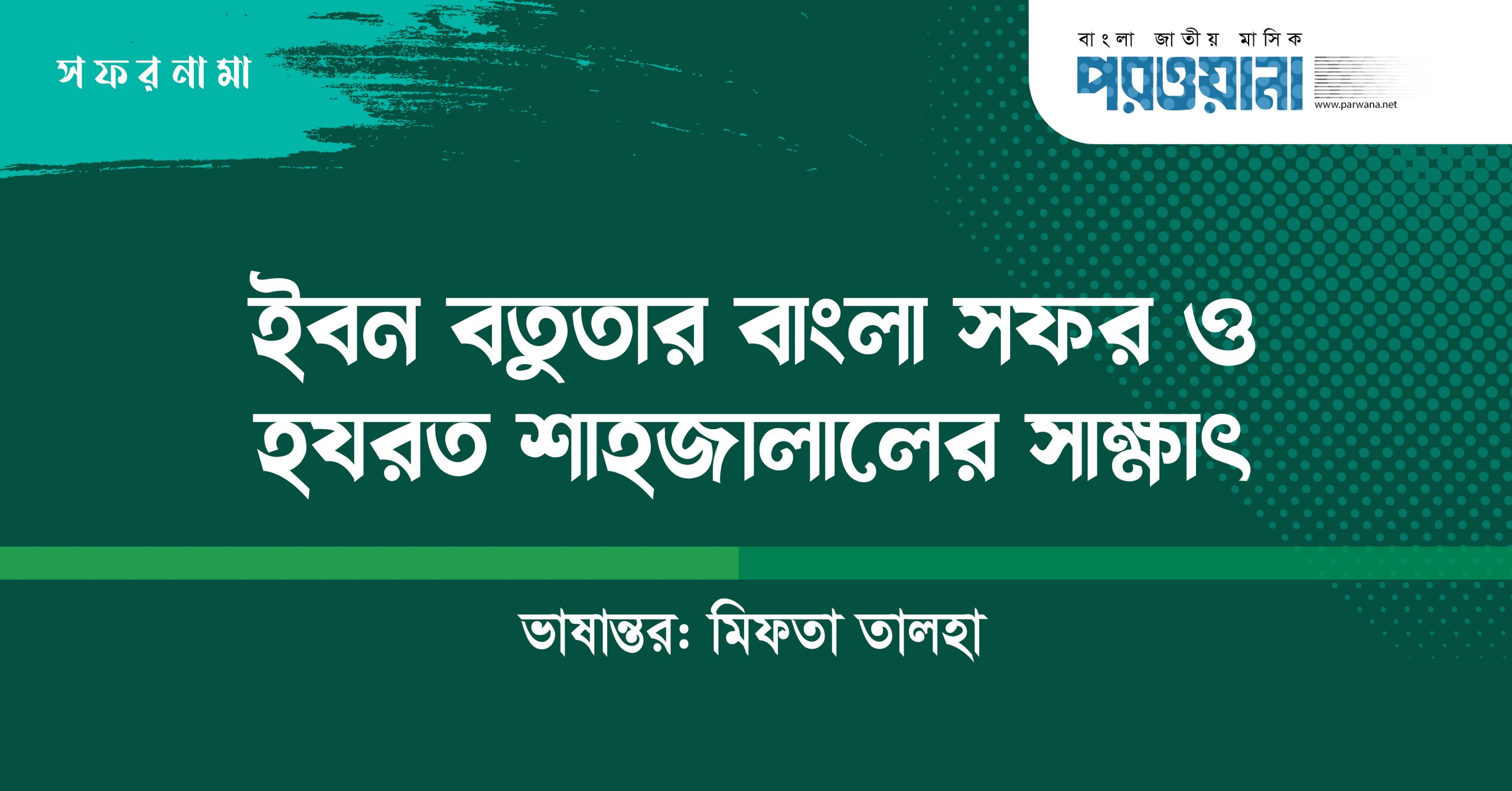গত আগস্ট মাসে ৪ দিনের ভ্রমণে তুর্কি গিয়েছিলাম। উসমানী খিলাফতের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী ইস্তাম্বুল ও নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ কাপাদোকিয়া দেখতে দেখতে কীভাবে চারদিন ফুরিয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি।
একদা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইস্তাম্বুল। গত শতকে কামাল আতাতুর্কের আগ্রাসী ‘বি-ইসলামিকরণ’ তুর্কি থেকে ইসলামকে বিদায় করতে চেয়েছিল। খিলাফতের সূর্য অস্তমিত হওয়ায় লাখো মুসলমানের অন্তরে ইসলাম নীরবে কেঁদে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রচালিত সেক্যুলারিজমের দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বসেছিল শতাব্দীপ্রাচীন ইসলামী ঐতিহ্য। আযান বদলে যায় তুর্কি ভাষায়, মাদরাসা গুম হয়ে যায় ইতিহাসের পাতায়, পীর-মুরশিদের আসর হয় নীরব। কিন্তু এই শীতল নিস্তব্ধতার ভেতরেই এক আশ্চর্য উষ্ণতা বয়ে আনেন কিছু সূফী বুযুর্গ—যাঁরা হঠাৎ বজ্রপাতের মতো নয়, বরং চুপিচুপি নামেন শিশিরের মতো। এই নিঃশব্দ বিপ্লবের অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী, যিনি অস্ত্র নয়, তুলে নেন কলম। তাঁর রচিত রিসালা-ই-নূর কেবল একটি গ্রন্থমালা নয়; এটি ছিল এক চেতনার বিপ্লব, যেখানে কুরআনের আলো, যুক্তির ধারা ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা মিলেমিশে নতুন প্রজন্মকে ইসলামের আলোয় ফিরিয়ে আনে। নিষিদ্ধ পরিবেশেও এই রিসালা হাতে হাতে, কপি করে, গোপনে পাঠ করে বহু তরুণ ইসলামের দিকে ফিরে আসে। তাঁর ছাত্র হুসাইন আতাই এবং জুবায়ের গুণদুয এসব নীরব মুজাহিদরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেন দাওয়াহর আলো। অন্যদিকে, নকশবন্দী তরীকার সূফীরা সমাজের গভীরে অনুপম ধৈর্য নিয়ে কাজ করে যান। তাঁরা রাজনীতি পরিহার করে মানুষের আত্মা গঠনে মনোযোগ দেন। মনে করিয়ে দেন, ইসলাম শুধু রাষ্ট্র নয়, বরং রূহের রাজত্ব। ইসমাইল আগা’র নেতৃত্বে ইস্কিলিপ ও বুরসার মতো শহরে তরবিয়ত কেন্দ্রে বহু যুবক তাযকিয়ার পথে চলতে শুরু করে। আধুনিক তুরস্কে মাহমুদ আফেন্দি’র মতো মুরশিদের নেতৃত্বে আফেন্দি আন্দোলনও এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসমাইল আগা জামাআত থেকে শুরু হয় হিজাব-পারদা, সুন্নাহ, মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম। হাজার হাজার নারী-পুরুষের জীবনধারা পালটে যায়, যাঁরা আগে রাষ্ট্রীয় প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত ছিলেন। তুর্কি রাষ্ট্রযন্ত্র যখন ইসলামকে ইতিহাসের জাদুঘরে বন্দি করতে চেয়েছিল, তখন এই সুফী আলিম ও বুযুর্গরা এক অনন্য ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন: ইসলাম কেবল এক ধর্ম নয়, বরং এক চেতনা, যা শত চাপেও মুছে যায় না। আজ ইস্তাম্বুলে আযান আরবীতে ফিরে এসেছে, মসজিদগুলো প্রাণ ফিরে পেয়েছে, ইমাম হাতিপ স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে, কুরআনের হিফয প্রতিযোগিতা হয় টেলিভিশনে এবং তার পেছনে আছে সেসব নিঃশব্দ মুজাহিদদের দীর্ঘশ্বাস, যাঁরা তাওবাহ ও যিকরের মাধ্যমেই ইতিহাস রচনা করেছেন।
তবে দ্বীনি পরিসরে ইসলাম ফিরলেও শহুরে সামাজিক আড্ডা ও আর্থিক লেনদেনে ইসলাম ফিরতে এখনও সম্ভবত দেরি আছে। গত কয়েক দশক ধরে ইসলামী ঐতিহ্য পুনর্জাগরণের চেষ্টার বেশ সফল হলেও তুর্কিবাসীর চলনে-বলনে পশ্চিমা সংস্কৃতি খুব শক্তভাবেই গেঁথে আছে। বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও ইউরোপ-এশিয়ার মধ্যখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে তুর্কিতে সারাবছর পশ্চিমা পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। এদের দ্বারা তুর্কিবাসী যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। বলা যায়, তুর্কি ইসলামী ঐতিহ্য ও পশ্চিমা আধুনিকতা, তথা সুলতান আবদুল হামিদ ও কামাল পাশার আদর্শের মাঝে এখনও দুলছে। মসজিদ-মাদরাসা আমাদের চেয়েও মশগুল; আবার বাজারগুলো ইউরোপের মতো মত্ত।
ইস্তাম্বুলে একদিন গেলাম আয়া সোফিয়া দেখার জন্য। দেড় হাজার বছর ধরে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) ছিল পূর্ব রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের রাজধানী। ৫৩৭ সালে এখানে নির্মিত হয় তৎকালীন রোমান খ্রিস্টানদের প্রধান ক্যাথিড্রাল আয়া সোফিয়া। ১৪৫৩ সালে অটোমান সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ অবিস্মরণীয় এক অভিযানে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন এবং আয়া সোফিয়া মসজিদে রূপান্তর করেন। ভেতরে গেলে বিশ্বাস হয় না, দেড় হাজার বছর আগে এত বিশাল, অসাধারণ স্থাপত্য মানুষ কীভাবে তৈরি করল! আকাশচুম্বী গম্বুজ, মার্বেলের দেয়ালে খোদাই করা খ্রিস্টান ধর্মের চিত্র, রঙিন মোজাইকের চোখধাঁধানো সব কারুকার্য, উসমানী আমলের মিনার সব মিলিয়ে আয়া সোফিয়া মানুষের অপার সক্ষমতার এক জীবন্ত সাক্ষী। এরপর ঘুরে দেখেছি তপকাপি প্যালেস। দীর্ঘ চারশ বছর এটি ছিল অটোমান সুলতানদের রাজপ্রাসাদ ও প্রশাসনিক কার্যালয়। ৪টি কোর্টইয়ার্ডে ভাগ করা তপকাপি বহু শতাব্দীর ইতিহাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম ৩০ জন অটোমান সুলতান এই প্রাসাদেই থাকতেন। ১৮৫৬ সালে সুলতান আবদুল মাজিদ ভাবলেন, তপকাপি যথেষ্ট আধুনিক নয়। তাই তিনি ইউরোপীয় ডিজাইনে নতুন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, নাম দোলমাবাহচে প্যালেস। মুসলিম সুলতানদের এসব বিলাসিতার গল্প শুনতে আজ অসহ্য লাগে। কাড়িকাড়ি পয়সা ঢেলে আয়েশি প্রাসাদ না বানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও সময়োপযোগী অস্ত্র বানালে ইউরোপীদের কাছে এত সহজে ধরাশায়ী হতে হতো না। এক সময় সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলীদের কাছ থেকে যুগোপযোগী অস্ত্র বানিয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেছিলেন। অথচ পরবর্তী সুলতানরা বিলাসিতার কারণে সালতানাতের প্রশাসনিক সংহতির দিকে খেয়ালই করতে পারেননি। তার ওপর অটোমানদের ‘প্রাসাদ-রাজনীতি’ তো ছিলই; যা সালতানাতকে ভেতর থেকে দুর্বল করে এক সময় ‘ইউরোপের রুগ্ন মানুষে’ পরিণত করেছিল।
প্রাসাদের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। ইউরোপের অনেক দেশে বহু রাজপ্রাসাদ আমি দেখেছি। আমি তপকাপিতে গিয়েছিলাম অন্য কারণে। তপকাপির একটি ভবনে আমাদের প্রিয় নবী e এর চুল, দাড়ি, লাঠি, তরবারি, জুতা এবং সাহাবায়ে কিরামের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। মুবারক এই স্মৃতিচিহ্নগুলোর সামনে দাঁড়ানোমাত্র পাপি চোখ পানিতে ভিজে গেল।
ইস্তাম্বুল দুই মহাদেশের মাঝে ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বয়ে চলছে বসফরাস প্রণালি (Strait of Bosphorus)। একপাশে তার এশিয়া, একপাশে ইউরোপ। বসফরাস থেকে উত্তরদিকে Golden Horn নামে এক শাখানদী বের হয়েছে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের সময় এখানকার রোমান সৈন্যরা লোহার চেইন ফেলে গোল্ডেন হর্ন আটকে দিয়েছিল, যেন মুসলমানদের জাহাজগুলো গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে না পারে। সুলতান মুহাম্মদের নির্দেশে মুসলিম সৈন্যরা কয়েক মাইল মাটির রাস্তার ওপর তক্তা বিছিয়ে, তাতে চর্বি ফেলে তক্তার ওপর দিয়ে নিজেদের জাহাজগুলো ঠেলে নিয়ে গোল্ডেন হর্নে পৌঁছে গিয়েছিল। রোমানরা ভেবে পাচ্ছিল না, মুসলমানরা জিন না মানুষ! আসলেই, কনস্টান্টিনোপল বিজয় ছিল মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক অধ্যায়। ফেরিতে চড়ে দীর্ঘ সময় বসফরাস ও গোল্ডেন হর্ন ভ্রমণ করেছি। স্মৃতিতে ভেসেছে মুসলমানদের সেই গৌরবময় দিনগুলোর দৃশ্য। কবে আবার আমাদের ওই হারানো ইযযত ফিরে আসবে, জানি না। এই সে ইস্তাম্বুল–গালাটা টাওয়ার, অটোমানদের দুর্ভেদ্য দুর্গ, ব্লু মসজিদ; ওইপাশে উসকুদার, কাদিকয়, সিরকেজি; এপাশে ফাতিহ, তাকসিম; মাঝখানে বসে চলছে অক্লান্ত বসফরাস। সবই আছে; শুধু আমাদের খিলাফত নেই!
তুর্কি সফরের একটি রূহানী অভিজ্ঞতা ছিল রাসূল e এর মেজবান আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) এর যিয়ারত। মহান এই সাহাবী বেশ কয়বার ইস্তাম্বুল অভিযানে শরীক হওয়ার পর ৬৭৪ সালে শহরের ঠিক পাশে ইন্তিকাল করেন। দ্বীনের প্রতি কতটুকু মমতা থাকলে এক বৃদ্ধ সাহাবী মদীনা থেকে এতদূরের ইস্তাম্বুলে এসে সমাহিত হতে পারেন, ভেবে পাই না।
একদিন গিয়েছিলাম বহুদুরের কাপাদোকিয়া শহরে। ইস্তাম্বুল থেকে বিমানে প্রায় দেড় ঘন্টার জার্নি, এরপর মাইক্রোবাসে করে আরও প্রায় এক ঘন্টা। তর্কির নেভশেহের প্রদেশে অবস্থিত কুদরতের এক অদ্ভুত লীলা এই কাপাদোকিয়া শহর। নয়নাভিরাম সব পাহাড়, বিশাল বড় বড় উপত্যকা, আর সিমসাম একটি পর্যটন এলাকা। কাপাদোকিয়ায় পাথরের পাহাড়গুলো চিমনির মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোকে ফেইরি চিমনি বলা হয়। মাঝখানে বিশাল উপত্যকা। মনে হয় প্রাচীন রূপকথা থেকে উঠে আসা কোনো নগরী। ঘুরে ঘুরে লাভ ভ্যালি, পিজন ভ্যালি, প্যানোরেমা প্রমুখ অনেক পাহাড়-পর্বত দেখা হলো। পরদিন আবার ফিরে এলাম ইস্তাম্বুল।
ইস্তাম্বুলে এসে মিশেছিল পূর্ব-পশ্চিমের অর্থনীতি। সুপ্রাচীন গ্রান্ড বাজার ও স্পাইস বাজার সুলতানি অর্থনীতি ও সমৃদ্ধ ব্যবসার প্রমাণ বইছে। মসলার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। মিশরের মসলার বাজারে আমি ঘুরেছি, কাতারেও মসলার বাজারে ঘুরেছি। তবে ইস্তাম্বুলে মসলার বাজার অতুলনীয়। কায়েনাতে যত রঙ আছে, ইস্তাম্বুলের স্পাইস বাজারে সেই সব রঙের মসলা পেয়ে যাবেন। ইস্তাম্বুলের অলিতে-গলিতে দেখতে পাবেন মায়াকাড়া চেহারার শতশত বিড়াল। বলা হয়, বিড়ালগুলো ইস্তাম্বুলের নাগরিক। ইস্তাম্বুল সফরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, শহরটি অসম্ভব খরুচে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে পানির মতো টাকা খরচ হয়। শহরজুড়ে জালের মতো বিছানো মেট্রোরেলের লাইন। তবে কোন ট্রেন কোনদিকে যায়, সেটি বুঝতেও সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। সব মিলিয়ে ইস্তাম্বুল অনন্য, সমৃদ্ধ। তবে ইস্তাম্বুল বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, ফেলে আসা দিনগুলো ছিল সম্মানের।
সেপ্টেম্বর মাসে সাত দিনের সফরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘুরে এলাম। মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈদে মিলাদুন্নবী e উপলক্ষ্যে কয়েকটি মাহফিলে শামিল হওয়া। জার্মানি থেকে নেদারল্যান্ডস হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলাম। আমস্টারডামে ৪ ঘন্টার মধ্যবিরতি বাদ দিয়েও প্রায় সাড়ে ১২ ঘন্টার জার্নি। দীর্ঘ আকাশপথ পাড়ি দিয়ে দুনিয়ার প্রায় উত্তরপ্রান্ত থেকে প্রায় দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছালাম। জুহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে নেমে ছয় ঘন্টা গাড়ি চড়ে প্রথমে গেলাম ওয়ারিন্টন শহরে। শহরটি বিশেষত্বহীন, দেখার কিছু নেই। ওয়ারিন্টিনে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ওখানে আনজুমানে আল ইসলাহ দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক আয়োজিত মীলাদুন্নবী মাহফিল ছিল। দুদিন ওখানে থেকে তৃতীয় দিন গেলাম পাশের শহর কিম্বার্লি। কিম্বার্লিতে আছে মানুষের হাতে খনন করা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ প্রাকৃতিক হীরার খনি Big Hole. কুদরতের অপার দান ও মানুষের অন্তহীন লোভের সাক্ষী এই হীরার খনি। ১৮৬৬ সালে এখানে হীরা পাওয়া গিয়েছিল। হীরার ঝলকানি খুব দ্রুতই ইউরোপের লোভী ব্যবসায়ীদেরকে কিম্বার্লিতে টেনে আনে এবং শুরু হয় কালো মানুষের ওপর নির্মম শোষণ। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক এই খনিতে খনন করে আর পশ্চিমা লোভী ব্যবসায়ীরা এগুলো দিয়ে মুনাফা কামায়। বিশেষ করে রোডস নামক এক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সে সময় হীরার সবচেয়ে বড় কারবারি হয়ে উঠেছিল, যাকে ফাইন্যান্স করেছিল ধনাঢ্য ইয়াহুদী রথচাইল্ড পরিবার। প্রায় ২৮শ কেজি হীরা উত্তলনের পর ১৯১৪ সালে বিগহোল বন্ধ করে দেওয়া হয়। খনির পাশেই জাদুঘর। জাদুঘরে সে সময়ের পরাধীন কালো শ্রমিকদের ওপর ইউরোপের ধনীদের নিপিড়নের ছবি দেখে চোখে সয় না।
কিম্বার্লি থেকে ১৪ ঘন্টা বাসে চড়ে গেলাম কেপটাউন। এত পরিপাটি শহর আমি কম দেখেছি। চারদিন ছিলাম ওখানে। কেপটাউনে ভারত মহাসাগরের সাথে মিশেছে আটলান্টিক। অনিন্দ্যসুন্দর এই শহরটির একপাশে টেবিল মাউন্টেন, ডেভিল’স পিক, লায়ন্স হেট’র মতো উঁচু পাহাড়চূড়া, অপর পাশে সুবিশাল দুটি মহাসাগর। পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচের দিকে চোখ গেলে সাগরের গাঢ় নীল জলরাশি চোখে পড়ে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পীর তুলিতে আঁকা কেপটাউন। কুদরতের এই অকৃপণ দানের অপূর্ব রূপ মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করা বোকামি; তবু কয়টি ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি।
একদিন গেলাম আফ্রিকা মহাদেশের সর্ব-দক্ষিণপ্রান্তে, নাম Cape of Good Hope. শহর থেকে বেশ দূরে, ইউরোপের দুঃসাহসী অভিযাত্রী ও সাম্রাজ্যবাদীদের কাহিনী বুকে নিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে আছে ‘কেপ অব গুড হোপ’। ১৪৫২ সালে মুসলমানরা ইস্তাম্বুল বিজয় করার পর ইউরোপীয়দের জন্য ভূমধ্যসাগর হয়ে এশিয়ায় আসা ঝুকিপূর্ণ হয়ে যায়। অন্য একটি সাগরপথের খুঁজে ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা ইউরোপ থেকে জাহাজে চড়ে আটলান্টিক হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে নেমে, ‘কেপ অব গুড হোপ’ ঘুরে আবার উত্তর-পূর্বদিকে উঠে ইন্ডিয়াতে পৌঁছান। পরে এই পথে ইউরোপের অন্য সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়াতে এসেছিল। কেপ পয়েন্টের চূড়ায় জাহাজকে পথ দেখানো জন্য একটি লাইটহাউজ আছে। সেই চূড়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছি, যার পরে দক্ষিণে আর কোনো মানব বসতি নেই। কেপ পয়েন্টের পর আটলান্টিক মহাসাগর, এরপর দক্ষিণ মহাসাগর, এরপর এন্টার্কটিকা মহাদেশ।
দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের অবস্থান অমুসলিম দেশে আমার দেখা সবচেয়ে সমৃদ্ধ। জুহানেসবার্গ, কেপটাউন ও ডারবান প্রমুখ বড় শহরে মসজিদ-মাদরাসার কমতি নেই। এককালে ভারতের পশ্চিম তীর (গুজরাট ও মুম্বাই) থেকে প্রচুর ইমিগ্রেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান। এছাড়াও আরবের দক্ষিণ দিক তথা ইয়ামান থেকেও বহু মুসলমান এদেশে মাইগ্রেট করেছিলেন। এখন এদের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ প্রজন্ম চলছে। সে তুলনায় বেশিরভাগ বাংলাদেশি এখনও প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ইমিগ্রেন্ট। তাই “দক্ষিণ আফ্রিকান মুসলিম” মানে মূলত পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ আরবের মুসলমান, যারা বহু প্রজন্ম ধরে এই দেশকে নিজেদের ঘর বানিয়েছেন। এদের দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা হয়েছে। ব্যবসা, সমাজ, রাজনীতি সর্বত্রই তাঁরা সংখ্যানুপাতিকহারে মোটামুটি প্রভাবশালী। জুহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে ইউসুফ নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকান ভদ্রলোকের সাথে কয়েক ঘন্টা আলাপ হয়। তিনি এসব তথ্য আমাকে দিয়েছেন। ভারতীয় ও আরব বংশদ্ভূত মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য আফ্রিকান দেশের মুসলমানরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করে। এরা মূলত আসে কাজের সুবাদে। যদিও প্রথম প্রজন্মের ইমিগ্রেন্টদের দ্বারা বেশি কিছু আশা করা যায় না (যেহেতু তারা এখনও স্যাটলড নয়), এরপরও বাংলাদেশি মুসলমানরা এখানে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েকটি মসজিদ-মাদরাসায় আমরা মাহফিল করেছি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কেপটাউনে সিলেটি ছাড়াও অন্যান্য বাংলাদেশি এবং ফুলতলী মাসলাকের বাইরের লোকেরাও ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর নাম শুনে আগ্রহী হয়ে আমাদের মাহফিলগুলোতে শরীক হয়েছেন। কেবল শরীক হয়েছেন বললেও ভুল হবে। আমর দুটি মাহফিল করার পর বাকি দুটি ঘরোয়া মাহফিল তাঁরাই আয়োজন করেছেন। ভবিষ্যতে কেপটাউনে আনজুমানে আল ইসলাহ’র কার্যক্রম পরিচালনা ও দারুল কিরাতের ব্যাপারেও সবার সাথে কথা হয়েছে।
তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সবকিছু যেন এসে থমকে যায় ভয়াবহ দুর্নীতি ও সীমাহীন অপরাধে। দক্ষিণ আফ্রিকা গ্যাং ওয়ার, চুরি-ডাকাতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির আখড়া। এত সুন্দর একটি দেশ, অথচ অপরাধের সীমা নেই। পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খাওয়ার জন্য হা করে থাকে। এরকম এক কর্মকর্তা আমাকে অন্যায়ভাবে বিপদে ফেলেছিল। ঘুষ খাওয়ার জন্য আমার পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে দুই-তিন ঘন্টা রেখে দিয়েছিল, যার আইনত অধিকার তার নেই। দুই-তিন ঘন্টা প্রচণ্ড পেরেশানিতে কেটেছে। তবে এই দুঃসহ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা সফর আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা কুদরতের অপরূপ দান, পরাধীন-শোষিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলা একটি সাহসী রাষ্ট্র। এই দক্ষিণ আফ্রিকা বর্বর ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে এবং নিজ খরচে মামলা লড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান ও খ্রিস্টানরা একজোট হয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রটেস্ট করেন। এরকম সাহসী অবস্থান বেশিরভাগ মুসলিম রাষ্ট্রেও দেখা যায় না। এদিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের শ্রদ্ধা পাওয়ার হকদার।